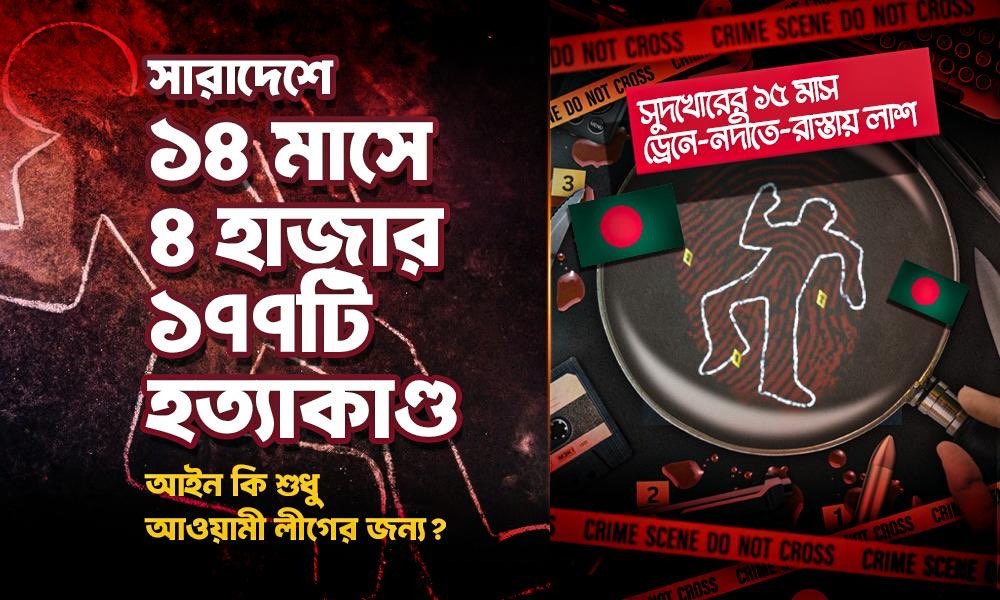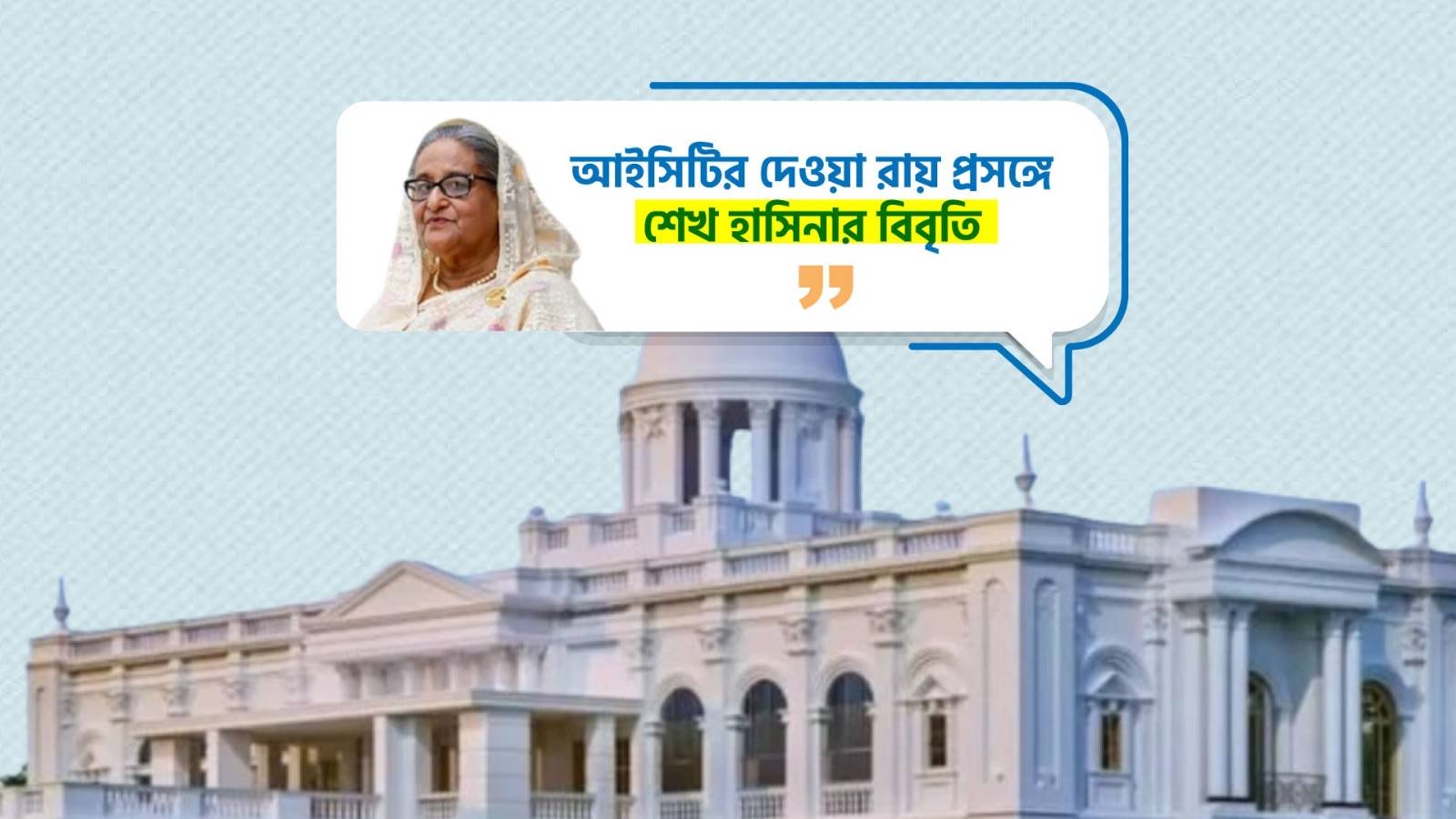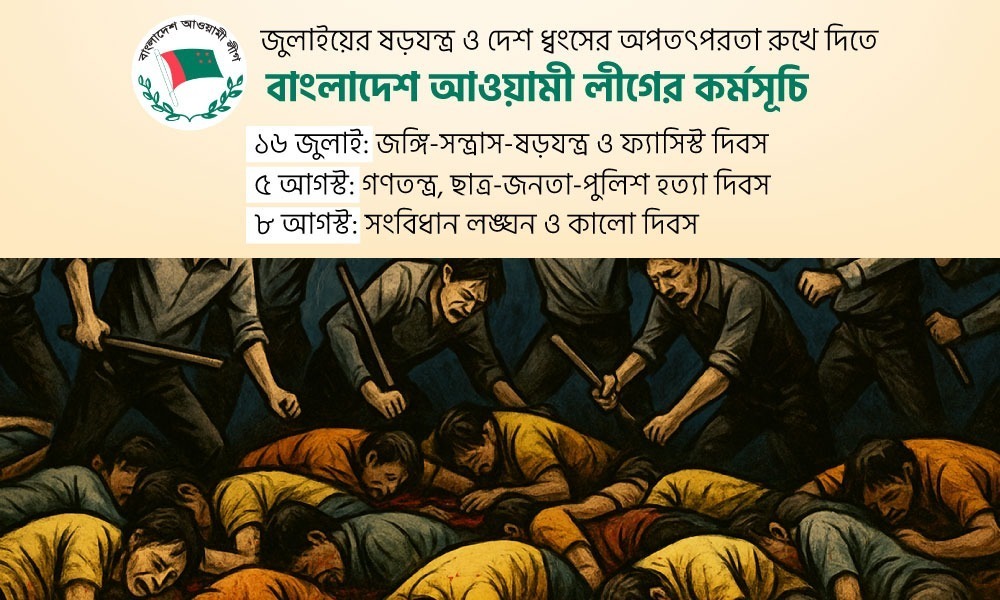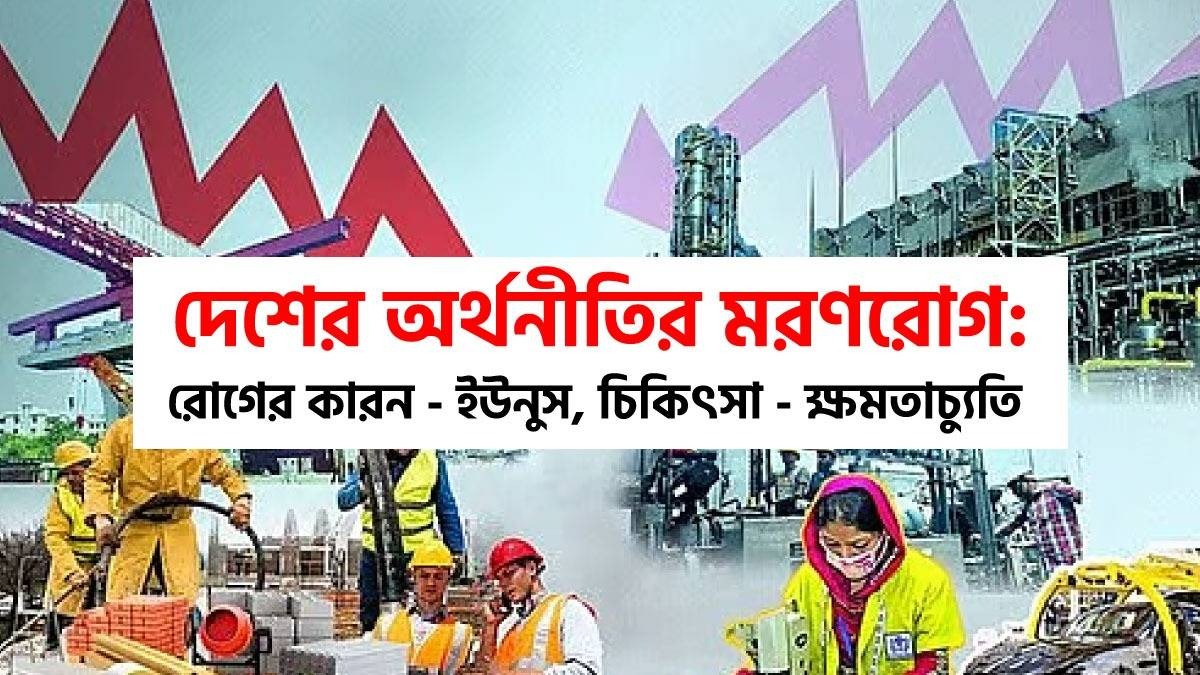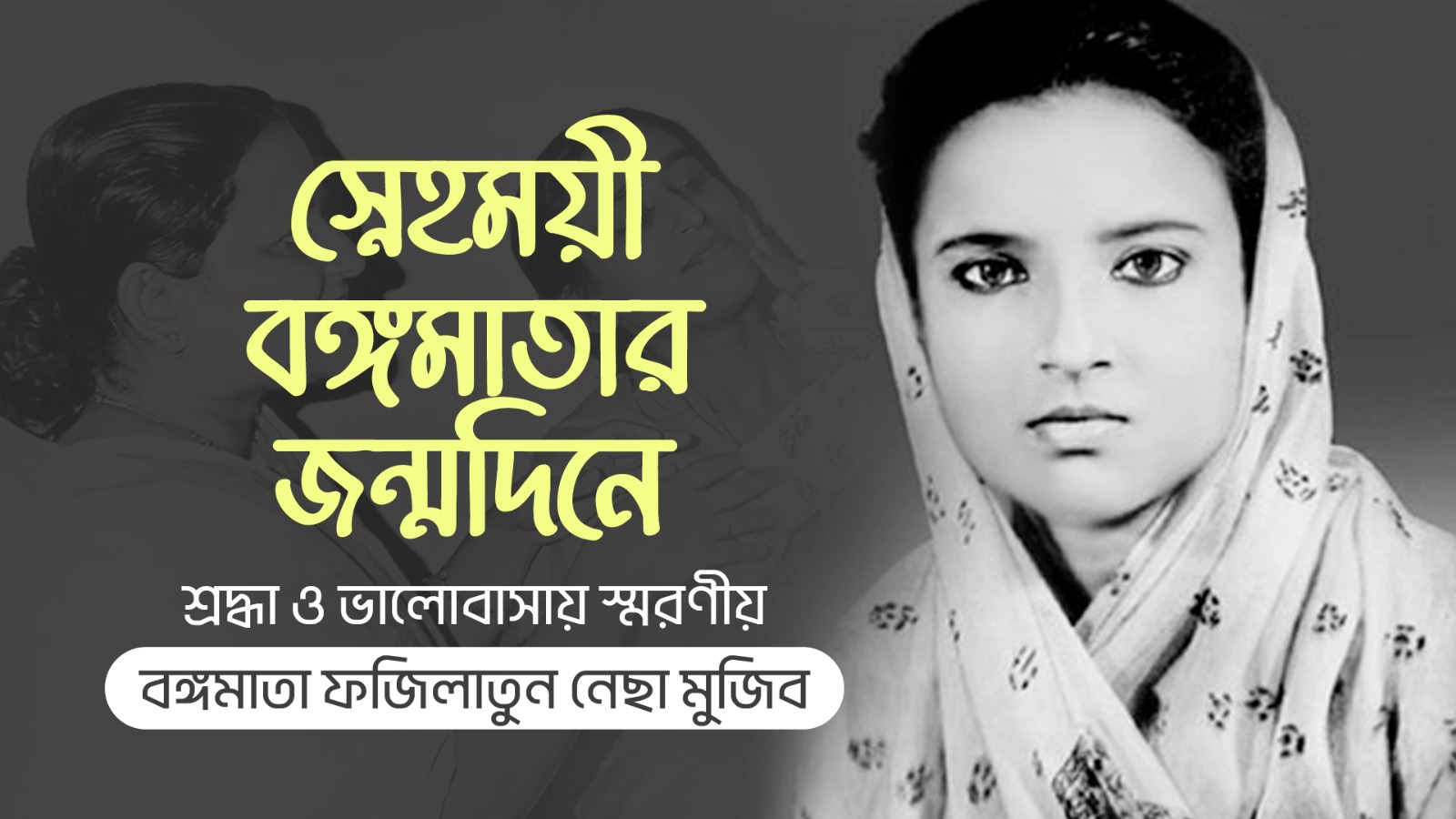2034
Published on আগস্ট 28, 2025২০২৫ সালের বাংলাদেশ আর গণতান্ত্রিক দেশ নয়। এটি এখন ভয়, সহিংসতা ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকলে আবদ্ধ দেশ। মুহাম্মদ ইউনূসের অবৈধ অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে স্বাধীনতার অঙ্গীকার রূপ নিয়েছে নির্যাতনের এক দুঃস্বপ্নে। মানবাধিকার শুধু লঙ্ঘিতই হচ্ছে না, বরং ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।
সাংবাদিকদের অপরাধীর মতো ধরা হচ্ছে, অ্যাক্টিভিস্টদের রাষ্ট্রের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, আর সাধারণ মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে—কারণ এখন ন্যায়বিচার নির্ধারণ করছে জনতা ও উন্মত্ত গোষ্ঠী।
মানবাধিকার কি মুহাম্মদ ইউনূসের শাসনে হুমকির মুখে?
যে প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণকে রক্ষা করার জন্য ছিল, সেগুলো ভেঙে পড়েছে। আদালত জনতার চাপে নতি স্বীকার করছে, পুলিশ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, আর সেনাবাহিনী নীরব দাঁড়িয়ে আছে। দেশ যখন অরাজকতার গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে, তখনও তারা হস্তক্ষেপ করতে চাইছে না। আইন নয়, ভয় এখন শাসন করছে, আর ভিন্নমতের মানুষগুলোকে শুধু কারাগার যেতে হচ্ছে বরং তাদের গুম, নির্যাতন, কিংবা মৃত্যুর শিকার হতে হচ্ছে।
এটি শাসন নয়; এটি দমন। এটি গণতন্ত্র নয়; এটি স্বৈরাচার—যা আন্তর্জাতিক প্রশংসার ভুয়া বৈধতার আড়ালে ঢাকা। আর আজকের বাংলাদেশে সত্য বলা মানেই সবকিছু ঝুঁকির মুখে ফেলা। কারণ সত্য নিজেই সেখানে অপরাধে পরিণত হয়েছে।
অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন
বাংলাদেশে এখন সত্য বলা এক সাহসী এবং একইসঙ্গে বিপজ্জনক কাজ। সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীদের হয়রানি, বেআইনি গ্রেপ্তার এবং গুম নজিরবিহীন মাত্রায় পৌঁছেছে। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত ৪৯৬ জন সাংবাদিক হয়রানির শিকার হয়েছেন, আর দায়িত্ব পালনের সময় প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন। অসংখ্য গণমাধ্যমকর্মী প্রতিনিয়ত হুমকি, আদালতের সমন ও ভয়ভীতির মুখে পড়ছেন। এতে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে সত্য উচ্চারণ করলে হতে পারে মৃত্যু।
এক বছরে ৪৯৬ সাংবাদিক হয়রানির শিকার
২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর দমন-পীড়ন আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। সাংবাদিক ও লেখকদের জোরপূর্বক আদালতে টেনে নেওয়া হয় মনগড়া হত্যা ও হামলার মামলায়, যেসব ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনো সংশ্লিষ্টতাই ছিল না। ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রামসহ দেশের অসংখ্য জেলায় অভিজ্ঞ ও স্থানীয় প্রতিবেদকদের গায়েবি মামলায় জড়ানো হয়। এগুলোর অধিকাংশই অতীতের রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এসব মামলায় প্রায়ই দুর্বল বা পরস্পরবিরোধী ‘সাক্ষ্য’ ব্যবহার করা হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয়ে যে, এটি ছিল স্বাধীন চিন্তাকে অপরাধে পরিণত করা এবং গণমাধ্যমকে ভয় দেখানোর এক সংগঠিত প্রচেষ্টা।
দমন শুধু আদালত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। শত শত সাংবাদিকের প্রেস অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড বাতিল করা হয়, আর গণমাধ্যম অফিসগুলোতে হামলা চালানো হয় ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে। সম্পাদক ও সংবাদপ্রধানদের অপসারণ করা হয়, অন্তত ১৫০ জন সংবাদকর্মী চাকরি হারান। এতে সাংবাদিক সমাজের বড় একটি অংশ হয়ে পড়ে অসহায় ও স্তব্ধ। এমনকি সরকারি তথ্য পাওয়ার নিয়মিত পথও বন্ধ করে দেওয়া হয়। অন্তর্বর্তী সরকারও তথ্য অধিকার আইনের সংস্কারে প্রকাশ্য উদাসীনতা দেখিয়ে জনগণের মৌলিক জানার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে।
জনকণ্ঠ দখলের অভিযোগ, মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা
সোশ্যাল মিডিয়া এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এখন প্রোপাগান্ডার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। মিথ্যা সংবাদ, ছবি এবং গুজব পদ্ধতিগতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সাংবাদিক ও কর্মীদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার জন্য। এআই-সৃষ্ট কনটেন্ট ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ঘটনা গড়ে তোলার, বিভাজন সৃষ্টি করার এবং সুনাম নষ্ট করার জন্য। আর সরকার এতে নীরব ভূমিকা পালন করছে।
এই সবের মাঝেও সেনাবাহিনী অনুপস্থিত। যখন ছাত্র-জনতার নামে জঙ্গি, রাজনৈতিক কর্মীরা সাংবাদিকদের কোনরকম বাধা ছাড়াই হুমকি দেওয়া হচ্ছে তখনও তারা হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করছে। বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আর কোনো অধিকার নয়; এটি অপরাধ হিসেবে পরিণত হয়েছে। এটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে অনেকের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। প্রতিটি মিথ্যা অভিযোগ, প্রতিটি তল্লাশি, প্রতিটি চাকরি বাতিল—সবই এক ভয়ানক সত্যকে প্রমাণ করছে: ভিন্নমত প্রকাশ বিপজ্জনক, সত্য প্রকাশ বিপজ্জনক, এবং ভয়ই এখন জনজীবনের শাসন করছে।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নীরব ভূমিকা
বাংলাদেশ দ্রুত এমন এক সমাজে পরিণত হচ্ছে যেখানে নীরবতাই টিকে থাকার উপায়। আর সত্য উচ্চারণ করা মানে বিদ্রোহ। এর কারণে শাস্তি হয় হয়রানি, কারাবরণ, কিংবা আরও ভয়াবহ কিছু।
হাইজ্যাক হওয়া আদালত: উগ্রবাদী জনতার দখলে বিচারব্যবস্থা
বাংলাদেশে আদালত আর আইনের সেবা করছে না; এটি এখন ক্ষমতা ও ভয়ের সেবা করছে। যে আদালত নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা পরিণত হয়েছে ভয় দেখানো, ও অন্যায় শাস্তি দেওয়ার হাতিয়ারে। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে বিচারব্যবস্থাকে সুসংগঠিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সাধারণ নাগরিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী এবং যারা কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করার সাহস করছে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে।
দেশের বিভিন্ন জেলায় সাংবাদিক ও লেখকদের গায়েবি মামলায় জড়ানো হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে হত্যা থেকে শুরু করে হামলার অভিযোগ পর্যন্ত করা হচ্ছে। তবে এসব ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। অসংখ্য মানুষ অনির্দিষ্টকালের আইনি জটিলতায় আটকে আছেন, কারণ ব্যাপক হারে মামলা করা হচ্ছে দুর্বল বা পরস্পরবিরোধী প্রমাণের ভিত্তিতে। সাক্ষ্যগুলো পুনঃব্যবহার করা হচ্ছে, বিকৃত করা হচ্ছে, কিংবা একেবারেই তৈরি করে নেওয়া হচ্ছেশুধুমাত্র ভিন্নমতাবলম্বীদের টার্গেট করার জন্য। পুরো গণমাধ্যম এখন এক আতঙ্কের ছায়ায় বসবাস করছে, যেখানে অস্থিরতা নিয়ে প্রতিবেদন করাও এখন অপরাধী করে তোলে।
এ পর্যন্ত ২৬৬ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা
সাধারণ নাগরিকদের জন্য পরিস্থিতি মোটেও ভালো নয়। গোপালগঞ্জের মতো শহরগুলোতে নির্বিচার গ্রেপ্তার ও আটক আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। মাত্র ১২ বছর বয়সী শিশুদেরও সন্ত্রাসবিরোধী আইনে কারাগারে পাঠানো হয়েছে এমন অপরাধে, যা তারা করেনি।
পরিবারগুলো জানিয়েছে, গ্রেপ্তারের হুমকিতে তাদের ঘুষ দিতে বাধ্য করা হয়েছে বা পুলিশের দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। এমনকি দোকানদার, শিক্ষার্থী, স্থানীয় পেশাজীবী যারা কোনো রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা রাখেন না তারাও আইনি প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়েছেন শুধুমাত্র বিক্ষোভে উপস্থিত থাকার কারণে। আইন এখন আর সুরক্ষার ঢাল নয়; এটি পরিণত হয়েছে গণভীতি সৃষ্টির অস্ত্রে।
এদিকে, উন্মত্ত জনতা ও উগ্র গোষ্ঠীগুলো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা জানে আদালত তাদের জবাবদিহির আওতায় আনবে না। তাদের উসকানিমূলক বক্তব্য ও সহিংস কর্মকাণ্ড খুব কম ক্ষেত্রেই বিচার হয়। বরং হামলার শিকারদেরই চাপে ফেলা হয়, হয়রানি করা হয়, এবং দোষারোপ করা হয়। বর্তমানে আদালত নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে, ফলে নাগরিকরা রাজনৈতিক শক্তি ও তাদের সমর্থিত সন্ত্রাসীদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা নষ্ট করছে এবং এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করছে যেখানে আইন নয়, বরং ক্ষমতাই ফলাফল নির্ধারণ করছে।
বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপ হচ্ছে
বিচারব্যবস্থা কাজ করার চেষ্টা করলেও হস্তক্ষেপ ও ভয়ভীতি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এখন আইনজীবী, সাক্ষী এমনকি বিচারকেরাও হুমকির মুখে পড়েন, যাতে রায় সবসময় প্রভাবশালী বা বলপ্রয়োগকারীদের পক্ষে যায়। সহিংসতায় নিহতদের পরিবারগুলোকে যথাযথ ময়নাতদন্ত ছাড়াই দ্রুত কবর দিতে বাধ্য করা হয়, আর আইনি প্রক্রিয়াগুলোকে ব্যবহার করা হয় অপরাধীদের রক্ষার জন্য। বার্তাটি স্পষ্টঃ বাংলাদেশে শাসক বা তার মিত্রদের সাথে জোটবদ্ধদের জন্য দায়মুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।
সেনাবাহিনী যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে, ন্যূনতম আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অস্বীকৃতি জানায়—তখন নাগরিকরা থেকে যান অসুরক্ষিত। ওইদিকে আদালত অন্যায়ের সহযোগীতা করলে আর জনতা দায়মুক্তির নিশ্চয়তা পেয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় বলাই যায়, বিচারব্যবস্থা হাইজ্যাক হয়ে গেছে, আর ভয় এখন টিকে থাকার মুদ্রা।
ন্যায়বিচার, যা একসময় ছিল অঙ্গীকার, এখন পরিণত হয়েছে ভয় প্রদর্শনের এক নাট্যমঞ্চে। এটি এক অন্ধকার প্রদর্শনী যেখানে ভুক্তভোগীদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর অপরাধীরা মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ায়। বাংলাদেশের আদালত এখন অধিকার রক্ষার পরিবর্তে সন্ত্রাসের প্রয়োগকারী, ফলে জনগণ চিরস্থায়ী অনিরাপত্তা ও ভয়ের আবহে বসবাস করছে।
রাজনৈতিক সহিংসতা ও নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন
আজকের বাংলাদেশ এমন এক দেশে পরিণত হয়েছে, যেখানে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে সহিংসতা, আর ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা দিচ্ছে উন্মত্ত জনতা। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করার বদলে রাষ্ট্র সশস্ত্র গোষ্ঠী, রাজনৈতিক জনতা ও স্বঘোষিত প্রহরীদের হাতে রাস্তাঘাট ছেড়ে দিয়েছে। তারা বিরোধী কণ্ঠরোধ করছে এবং সাধারণ মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছে।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিষ্ক্রিয়তায় সাহসী হয়ে ওঠা বিরোধী গোষ্ঠী ও চরমপন্থীরা উন্মুক্তভাবে চালিয়ে যাচ্ছে ভাঙচুর ও হামলা। দেশজুড়ে বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শিকার করা হচ্ছে, আর “প্রতিশোধ”-এর নামে পাড়ায় পাড়ায় তল্লাশির চালানো হচ্ছে। এসব ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়; বরং এটি একটি বৃহত্তর, সুসংগঠিত আক্রমণের অংশ। এটি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে (সত্য বলা, সংগঠিত হওয়া, এবং ভয়মুক্তভাবে বেঁচে থাকা) পদ্ধতিগতভাবে ধ্বংস করছে।
পুরান ঢাকায় প্রকাশ্যে হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলার চিত্র উন্মোচন করছে
শান্তিপূর্ণ আন্দোলনও রেহাই পাচ্ছে না। ন্যায়বিচার বা জবাবদিহিতা দাবি করা বিক্ষোভকারীদের নিয়মিতভাবে সহিংসভাবে দমন করা হচ্ছে—কখনও সশস্ত্র জনতার হাতে, কখনও আবার রাজনৈতিকভাবে অনুগত পুলিশ ইউনিটের দ্বারা। নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের ওপর টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও লাঠিচার্জ চালানো হচ্ছে। আর সংগঠিত উন্মত্ত জনতা নির্বিঘ্নে বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন রূপ নিচ্ছে রক্তাক্ত আতঙ্কের দৃশ্যে—যেখানে প্রাণ হারাচ্ছে মানুষ, আর কণ্ঠস্বর চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।
ফলাফল হলো এমন এক দেশ, যেখানে স্বাধীনতার জায়গায় ভয় স্থান নিয়েছে। প্রতিটি নাগরিক জানে—রাজনৈতিক পরিচয়, ধর্মীয় পরিচয়, এমনকি একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টও তাকে টার্গেট বানিয়ে দিতে পারে। গণতন্ত্রের অঙ্গীকার ছিনতাই হয়ে গেছে সহিংসতার কাছে। আর বাংলাদেশের মানুষ হয়তো ভাবছে: যখন রাষ্ট্র নিজেই সরে দাঁড়ায়, তখন তাদের অধিকার রক্ষা করবে কে?
এখন নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের মাত্রা অবিশ্বাস্য। মুক্ত সমাবেশের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করলেই নাগরিকরা ভীতিপ্রদর্শনের শিকার হচ্ছেন। রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়ে প্রতিবেদন করার চেষ্টা করলেই সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষকে হয়রানি, গ্রেপ্তার বা গুমের মুখে পড়তে হচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো বিশেষভাবে অসহায়। তাদের মন্দির, উপাসনালয় ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলো আক্রমণের শিকার হচ্ছে—কর্তৃপক্ষ সেখানে চোখ বুজে থাকছে।
সবচেয়ে নিন্দনীয় হলো সেনাবাহিনীর নীরবতা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের নিষ্ক্রিয়তা। সহিংসতা বাড়তে থাকলেও জনগণকে রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হাত গুটিয়ে বসে আছে । এই সচেতন অস্বীকৃতি অপরাধীদের আরও সাহসী করে তুলছে, বার্তা দিচ্ছে যে জনতার সহিংসতাই এখন দেশের নতুন আইন।
উগ্রপন্থার উত্থান: অবরুদ্ধ নারীরা
জঙ্গিবাদ বিস্ফোরিত হয়ে এখন রূপ নিয়েছে নারীদের বিরুদ্ধে এক নির্মম অভিযানে। এটি এক এমন আক্রমণ, যা শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রতিদিনের জীবনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয়ে নেমে এসেছে। দুর্বল শাসনব্যবস্থা ও জনতার দৌরাত্ম্যে সাহসী হয়ে ওঠা উগ্র ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলো ধর্মকে অস্ত্র বানিয়েছে নারীর মর্যাদা, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা কেড়ে নিতে চাইছে। এর পরিণাম হলো এমন এক সমাজ, যেখানে নারীরা অবরুদ্ধ অবস্থায় বসবাস করছে শারীরিক সহিংসতা আর পদ্ধতিগত ভীতিপ্রদর্শনের দুই দিক থেকেই তাদের কোণঠাসা করে দেওয়া হচ্ছে।
বাংলাদেশি নারীর অধিকার উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরোধিতার শিকার: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ
দেশজুড়ে পাওয়া রিপোর্টগুলো এক ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরছে। এখন নারীরা টার্গেট হচ্ছেন শুধু রাজনৈতিক পরিচয় বা পেশাগত কারণে নয়, বরং কেবল উগ্র মতাদর্শের আরোপিত মানদণ্ডের বাইরে বেঁচে থাকার জন্যও। নারী শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীরা পোশাকের কারণে হামলার শিকার হয়েছেন, মত প্রকাশের জন্য হয়রানি সহ্য করেছেন, আর উগ্র মতবাদের বিরোধিতা করার জন্য মারধরের শিকার হয়েছেন। এমনকি সাধারণ রাস্তায় থাকা নারীরাও রেহাই পাচ্ছেন না; হয়রানি, হামলা ও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে নিয়মিত ঘটনা। এখানে টিকে থাকার অর্থ হলো নীরব থাকা।
গণ-অন্যায়ের উত্থান এই ভয়াবহতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। উগ্র গোষ্ঠীগুলো প্রকাশ্যে চালাচ্ছে তাদের নিজস্ব নৈতিক পুলিশি কার্যক্রম। যেখানে বাজার, বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি নিজেদের পাড়ামহল্লাতেও নারীরা লাঞ্ছিত ও আক্রান্ত হচ্ছেন। ভুক্তভোগীদের “অনৈতিক” বা “ইসলামবিরোধী” তকমা দেওয়া হচ্ছে, অথচ হামলাকারীরা থাকছে শাস্তির বাইরে। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চোখ বন্ধ করে থাকে, আর কখনও-কখনও অপরাধীদের পাশে দাঁড়ায়ও। নাগরিকদের রক্ষার বদলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রায়ই বেছে নিচ্ছে জঙ্গিদের সহায়তা করার পথ। তারা আক্রমণকারীদের রক্ষা করছে, অথচ ভুক্তভোগীদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে।
বাংলাদেশে নীতি পুলিশ ও নারীর ওপর সহিংসতার উত্থান
রাজনৈতিক ও উন্মত্ত জনতার প্রভাবেই আগেই ক্ষতিগ্রস্ত বিচারব্যবস্থা নারীদের সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করেছে। যৌন সহিংসতার শিকাররা এমন এক ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, যা তাদের আরও অপমান করছে। এ নিয়ে অভিযোগ দায়ের করলেই নতুন করে হয়রানি, হুমকি, আর ন্যায়বিচারের সামান্যতম আশাও ম্লান হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে নারীদেরকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছনার ভয় বা পরিবারের ওপর হামলার হুমকি দেখিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়েছে।
উগ্রবাদ, জনতার দৌরাত্ম্য আর রাষ্ট্রীয় উদাসীনতার এই বিষাক্ত মিশ্রণ নারীদের জনপরিসর থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং বহু দশকের লিঙ্গসমতার অগ্রগতি ভেঙে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, যেগুলো একসময় নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্র ছিল, এখন হয়ে উঠছে ভয়ের মঞ্চ—যেখানে নারী শিক্ষার্থীদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। পেশাজীবী নারীরা—সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিক্ষক—ক্রমশ জনজীবন থেকে সরে যাচ্ছেন, ইচ্ছাশক্তির অভাবে নয়, বরং প্রতিরোধের মূল্য এখন অনেক অসহনীয়ভাবে গেছে বলেই।
তারপরও ক্ষমতাসীনদের টনক নড়ছে না। তারা উগ্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। নারীদের সুরক্ষায় ব্যর্থ থেকে রাষ্ট্র কার্যত এই সহিংসতাকে অনুমোদন দিয়েছে। উগ্রবাদ মোকাবিলায় ব্যর্থতা এক জটিল বাস্তবতা তৈরি করেছে: নারীরা আর নিজেদের দেশেও নিরাপদ নন; তারা এমন এক ব্যবস্থায় আটকে আছেন, যা তাদের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করছে। তাদের জনজীবন থেকে মুছে দিতে চাওয়া শক্তিগুলোকে আরও সাহসী করে তুলছে।
বাংলাদেশের নারীরা কেবল চাপে নেই; তারা অবরুদ্ধ। তাদের অধিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো উগ্র শক্তিগুলো আর পিছিয়ে নেই, বরং প্রতিদিনের ভয়ের স্থপতি হয়ে উঠছে। আর প্রতিটি অদণ্ডিত সহিংসতা স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে: নারীর জীবন ও স্বাধীনতা মূল্যহীন।
মব সন্ত্রাস ও সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে হামলা
ভয় সৃষ্টির নতুন মাধ্যম হয়ে উঠেছে উন্মত্ত জনতা। আর জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাই তাদের সহজ শিকার। পুরো সম্প্রদায়গুলোকে আতঙ্কিত করা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায়, অথচ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা সেনাবাহিনী সামান্যতম হস্তক্ষেপও করছে না। জনতা হামলা চালালে রাষ্ট্র পিছিয়ে যায়, ফলে দুর্বল গোষ্ঠীগুলোকে সংগঠিত সহিংসতার দয়ার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়।
২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশে ২৫৮টি সাম্প্রদায়িক হামলা
রংপুরে হিন্দু পরিবারগুলো অসহায়ের মতো দেখেছে কীভাবে উন্মত্ত হামলাকারীরা তাদের বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে, লুট করেছে এবং ভেঙে ধ্বংস করেছে। এসব হামলা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ছিল না; বরং এটি ছিল সুসংগঠিত ভীতিপ্রদর্শনের অংশ। এসব একটি স্পষ্ট বার্তা যে দেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যারা প্রতিরোধ করার সাহস দেখিয়েছেন, তাদের পেটানো হয়েছে, আর অন্যরা পালাতে বাধ্য হয়েছেন। নিজেদেরকেই মাতৃভূমির ভেতরেই বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছে।
রংপুরে দুই হিন্দু পুরুষকে গণপিটুনিতে হত্যা
সহিংসতা ঘরবাড়িতেই থেমে থাকেনি। উপাসনালয় ও মন্দিরের মতো আধ্যাত্মিক আশ্রয়ের প্রতীকেও ভাঙচুর করা হয়েছে। সেগুলোকে অপবিত্র করা হয়েছে ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে। ভক্তদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, শতাব্দী-প্রাচীন ঐতিহ্য গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এমনকি সাংস্কৃতিক নিদর্শনও রক্ষা পায়নি। নারীশিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার ভাস্কর্য এবং মুক্তিযুদ্ধের শহীদস্মৃতি—যা একসময় ছিল আত্মত্যাগ ও পরিচয়ের প্রতীক—সেগুলোও টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা হয়েছে। এটি কোনো অন্ধ উন্মত্ততা ছিল না; বরং এটি ছিল সচেতনভাবে পরিচালিত সাংস্কৃতিক নিশ্চিহ্নকরণের এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা।
বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির ওপর একের পর এক সহিংসতা
এই হামলাগুলোকে আরও ভীতিকর করে তুলেছে নাগরিকদের রক্ষা করার দায়িত্বপ্রাপ্তদের নীরবতা। পুলিশ ইউনিটগুলো নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে থাকে, আর সেনাবাহিনী এগুলোর বিরুদ্ধে কোনো সুষ্ঠু চেষ্টা করেনি। এই সচেতন উদাসীনতা রাষ্ট্রকে অপরাধের অংশীদার করে তুলছে। রাষ্ট্র জনতাকে সংখ্যালঘুদের ওপর দমন চালাতে এবং দেশের ঐতিহাসিক স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য “সুবিধা” প্রদান করছে।
এসব ধ্বংসযজ্ঞ শুধু আইনশৃঙ্খলার পতন নয়; বরং এটি বহুত্ববাদ ও ন্যায়ের ধারণার ওপর পরিকল্পিত আক্রমণ। সংখ্যালঘুদের জনতার দৌরাত্ম্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার কার্যত এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস অভিযানের অনুমোদন দিয়েছে, যা দেশের নৈতিক কাঠামো চূর্ণ করে দিচ্ছে।
আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ: ন্যায়বিচার ও সুরক্ষার পথ
স্বাধীনতা হরণ, কণ্ঠরোধ, আর সর্বত্র ভয়ের পরিবেশে বাংলাদেশিরা নিরাপত্তা ও জবাবদিহিতার জন্য বিদেশের দিকেই তাকাচ্ছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের উদাসীনতা, সেনাবাহিনীর নীরবতা, এবং উগ্রপন্থী ও জনতার সহিংসতার কারণে নাগরিকদের আশা কমে এসেছে যে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আইন, শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার পুনঃস্থাপন করতে পারবে। এই পরিস্থিতিতে, আন্তর্জাতিক মনোযোগ ও হস্তক্ষেপ আর ঐচ্ছিক নয়—এটি জরুরি।
জাতিসংঘ থেকে শুরু করে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বিশ্বের মানবাধিকার সংস্থাগুলো বারংবার বাংলাদেশের পরিস্থিতির অবনতি তুলে ধরেছে। তবুও, সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ছাড়া এই সতর্কবার্তাগুলো কেবল কাগজের উপরে লিখিত শব্দই থাকে।
এ অবস্থায় লক্ষ্যভিত্তিক বিদেশি হস্তক্ষেপ বিভিন্ন রকম হতে পারে: সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে কূটনৈতিক চাপ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা, এবং নাগরিক ও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক মনিটরিং মিশন।
বাংলাদেশিরা বৈশ্বিক সম্প্রদায়কে দেখছে। তারা আশা করছে যে বিদেশি সরকার, মানবাধিকার সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ার চাপ দণ্ডমুক্তির চক্র ভেঙে দিতে পারবে। তারা জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মতো মেকানিজমের দিকে তাকাচ্ছে। যাতে হয়রানির শিকার সাংবাদিক, অবরুদ্ধ নারী, এবং স্থায়ী ভয়ে থাকা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ন্যায়বিচার দাবি করা যায়।
আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ স্থানীয় নাগরিক সমাজ এবং মানবাধিকার রক্ষকদের ক্ষমতায়ন করতে পারে। তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং সুরক্ষা প্রদান করে করত পারে যেন তারা নিশ্চিন্তে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ নারীর অধিকারকর্মী, সাংবাদিক এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য। যাদের সংগ্রাম প্রায়ই বিশ্বের কাছে অজানা থাকে। তবে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।
বিদেশি হস্তক্ষেপ ছাড়া নাগরিকরা এক ভয়ঙ্কর বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছেন। এখানে প্রতিনিয়ত অধিকার হরণ, অনিয়ন্ত্রিত উগ্রবাদ, এবং সহিংসতার স্বাভাবিকীকরণ করা হচ্ছে। নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার এবং মৌলিক স্বাধীনতার পুনঃস্থাপনের জন্য বিশ্বের নজরই এখন বাংলাদেশের জনগণের শেষ আশা।